স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৭২ সালে দেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য দরকারি, অপরিহার্য ব্যয় মেটাতেই এই বাজেট। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ের জন্য তৈরি হয়েছিল বাজেটটি। বাজেটের আকার ছিলো ৮ কোটি ৬২ লাখ ৪৮ হাজার ২০৪ টাকা। এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে ৫৩টি বাজেট। এবারের বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে সাত লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। যা চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ৭ হাজার কোটি টাকা কম।
সোমবার (২ জুন) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করবেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এটি হবে দেশের ৫৪তম বাজেট এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট।
জানা গেছে, গতানুগতিক প্রক্রিয়ার বাইরে এ বছর অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে (রেকর্ড করা) আজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করবেন। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ বৈঠকে অনুমোদন শেষে তাতে সই করবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর অর্থ উপদেষ্টা বাজেট ডকুমেন্টস নিয়ে রামপুরার বিটিভি ভবনে যাবেন। সেখানেই রেকর্ড করা হবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। যা বিকাল ৩টায় সম্প্রচার করা হবে।
প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশ ঘাটতি বাজেট করে আসছে। এর ফলে ধার করে সরকারকে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করতে হয়। বৈদেশিক উৎস এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এসব অর্থ ধার করা হয়। বৈদেশিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক ঋণ, আর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকবহির্ভূত ব্যবস্থা থেকে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস হিসাবে ঋণ নেয়।
বৈদেশিক উৎস মূলত বৈদেশিক ঋণ। সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশ থেকে সহজ শর্তে ঋণ নেয়। বৈদেশিক উৎস থেকে বেশি ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে পারলে তা অর্থনীতির জন্য বেশি সহনীয়। কারণ, এতে সুদহার কম এবং পরিশোধে অনেক সময় পাওয়া যায়। যদিও এ জন্য নানা ধরনের শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন এখন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ কর্মসূচির মধ্যে আছে। এ জন্য অনেক শর্তও পূরণ করতে হচ্ছে।
অন্যদিকে সরকার দুই ভাবে দেশের ভেতর থেকে ঋণ নেয়। যেমন ব্যাংকিং-ব্যবস্থা ও ব্যাংকবহির্ভূত-ব্যবস্থা। ব্যাংকবহির্ভূত-ব্যবস্থা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি। এভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেয় সরকার। তবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশি ঋণ নেওয়ার দুটি বিপদ আছে। ব্যাংকিং-ব্যবস্থা থেকে সরকার বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি খাতের জন্য অর্থ থাকবে কম। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। আর ব্যাংকবহির্ভূত-ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিলে বেশি হারে সুদ দিতে হয়। এতে সুদ পরিশোধে সরকারকে বেশি পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হয়। এতে পরের অর্থবছরের বাজেট বেড়ে যায়।
ব্যক্তি যা পারেন না, সরকার কিন্তু তা করতে পারে। সরকার টাকা ছাপিয়ে বাজেট-ঘাটতি পূরণ করতে পারে। তবে এই পথে বাজেট-ঘাটতি পূরণ করার বিপদও আছে। এতে মুদ্রা-সরবরাহ বেড়ে যায় এবং মূল্যস্ফীতি তৈরি। এখন যে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছর আগে টাকা ছাপিয়ে সরকারকে দিয়েছে। ঘাটতি বেশি থাকাটা আবার ভালো নয়। সাধারণত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতিকে মেনে নেওয়া হয়।
অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, অব্যাহতভাবে সুষম বাজেট তৈরি করা ভালো কিছু নয়; বরং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বাজেট কেমন হবে তা ঠিক করা উচিত। কেননা, সুষম বাজেট সুদের হার কমায়, বাড়ায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। এ ছাড়া বাণিজ্যঘাটতি কমিয়ে আনে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতি এগিয়ে যায়।
সাধারণত অর্থনীতি ভালো অবস্থায় থাকলে সুষম বাজেট করা হয়, খারাপ হলে অর্থনীতিকে উদ্দীপনা দিতে তৈরি হয় ঘাটতি বাজেট। একটা সময় ছিল যখন ঘাটতি বাজেটকে ক্ষতিকর ও সরকারের দুর্বলতাও ভাবা হতো। পরিস্থিতি এখন পাল্টেছে; বরং অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে কিছুটা ঘাটতি থাকা ভালো। এতে অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহার বাড়ে, ঘাটতি পূরণের চাপ থাকে। তাতে অর্থনীতিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ঘাটতি বেশি থাকাটা আবার ভালো নয়। সাধারণত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতিকে মেনে নেওয়া হয়।
যদিও ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদি অর্থশাস্ত্রীরা ঘাটতি বাজেট অনুমোদন করতেন না। তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার একটি কৌশল হিসেবে ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে সম্পদ সংস্থানের ব্যবস্থাকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনসই প্রথম অনুমোদন করেন। তাঁর মতে অর্থব্যবস্থায় অপূর্ণ নিয়োগের সমস্যা দূর করতে হলে এবং মন্দাভাব এড়াতে হলে বাজেটে সমস্থিতি বজায় রাখলে কোনো কাজ হবে না। এর জন্য চাই ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করে নতুন আয় সৃষ্টি। এতে জাতীয় আয় বাড়ে এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৪ শতাংশের নিচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে, যা চলতি অর্থবছরের ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা এবং জিডিপির ৩ দশমিক ৬২ শতাংশ।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ; যা মহামারিকাল পরবর্তী সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। কৃষি খাতে ধীরগতির কারণেই এই পতন ঘটেছে। তবে আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। যা চলতি বছরের জন্য সংশোধিত ৫ দশমিক ২৫ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি।
চলতি অর্থবছরে এডিপির আকার যেখানে ছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা, সেখানে আগামী অর্থবছরে তা নামিয়ে আনা হচ্ছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়। বাজেট ঘাটতি ধরা হচ্ছে জিডিপির ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। এবার রাজস্ব বাজেটের আকার কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা , যা চলতি অর্থবছরের ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেশি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বারবার ভর্তুকি কমানোর ওপর জোর দিয়ে আসছে, তারপরও সরকার বিদ্যুৎ ও সার খাতে ভর্তুকি কিছুটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ হতে পারে প্রায় ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা।
অতীতের রাজনৈতিক সরকারের মতোই ঘাটতির অর্ধেকেরও বেশি বিদেশি উৎস থেকে এবং বাকিটা ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বাজেটে পরিচালন বা অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ধরা হতে পারে ৫ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা।


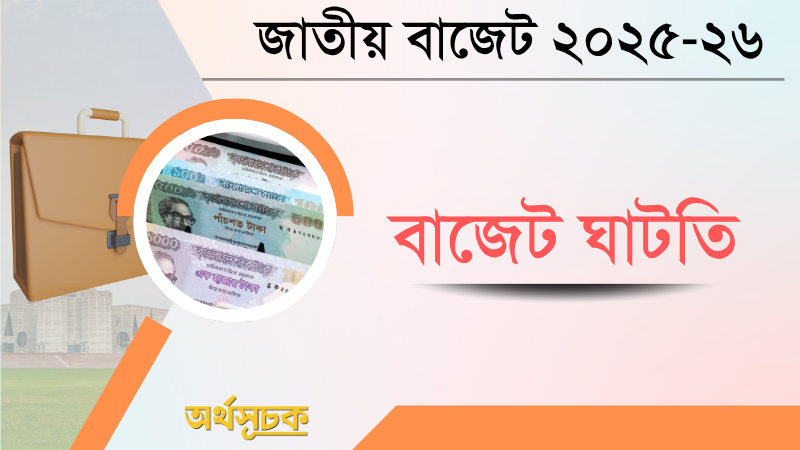

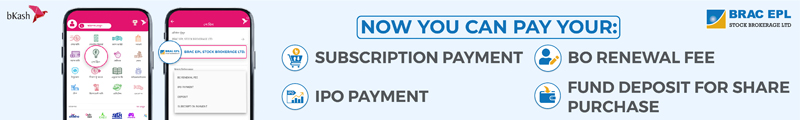
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.