সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং খাত একাধিক রেকর্ড ভেঙে মুনাফার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, বিশেষ করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে । ঋণের সুদ, স্থায়ী বিনিয়োগ থেকে আয়, নানাবিধ ফি ও সার্ভিস চার্জ এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন থেকে অর্জিত অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে এই লাভ অর্জিত হয়েছে । কিন্তু এই চিত্রের বিপরীত দিক হচ্ছে দেশের কর্পোরেট খাত, বিশেষ করে এসএমই, আমদানিকারক ও স্থানীয় উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো । তারা অধিকাংশই লোকসানে অথবা শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে । মন্থর অর্থনীতি, এনপিএল এর আধিক্য ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও ব্যাংকগুলোর মুনাফার উষ্ফলন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এই অসম লাভ ও ক্ষতির ব্যবধান কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং নৈতিক প্রশ্নও উত্থাপন করছে, ব্যাংকগুলো কি নিজেদের লাভের জন্য ক্লায়েন্টদের টিকে থাকার সক্ষমতাকে হুমকিতে ফেলছে?
ব্যাংকিং খাতে মুনাফার সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনের আলোকে নিচের বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়েছে:
- ঋণের সুদের আয় বেড়েছে ২০-২৫%, কারণ ৯% সুদের সীমা তুলে নেওয়ার পর ঋণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- ট্রেজারি বন্ড ও বিলের উপর আয় বেড়েছে, যেখানে কিছু মেয়াদের রিটার্ন ১১% পর্যন্ত উঠেছে। ঝুকিমুক্ত লাভের জন্য অলস ব্যাংকিং দেশের শিল্পায়নের অন্তরায় ।
- ফি ও চার্জ যেমন এলসি চার্জ, অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ফি, ডকুমেন্টেশন ফি ইত্যাদি ১৮-২২% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে লাভ একটি নতুন আয়ের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । ডলার-টাকার অনিশ্চয়তা কাজে লাগিয়ে বেশিরভাগ ব্যাংক আমদানিকারকদের কাছে প্রতি ডলারে ১ -৫ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ধার্য করার অভিযোগ রয়েছে । আমদানিকারকরা গত ৩/৪ বছর যাবৎ যেখানে ক্রমাগতভাবে ডলার রেটে লোকসান করছে সেখানে ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা দ্বিগুন করছে ।
এই সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় মিলিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেশিরভাগ টায়ার-১ ব্যাংকগুলো ঈর্ষণীয় মুনাফা অর্জন করেছে ।
কর্পোরেট খাত: টিকে থাকার সংগ্রামে
ব্যাংকিং খাত যেখানে শক্তিশালী মুনাফা দেখিয়েছে, সেখানে কর্পোরেট খাতের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন । ডলারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে আমদানিকৃত পণ্য ও কাঁচামালের দাম বেড়েছে ১৫-৩০% । কার্যকরী মূলধনের ঋণের সুদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩-১৫% । নানাবিধ চার্জ যেমন- হ্যান্ডলিং ফি, অ্যাডভাইসিং ফি, পেমেন্ট প্রসেসিং ফিস, পোর্টফোলিও মনিটরিং ফি, এলসি সংশোধন ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে যা মুনাফার হারকে সংকুচিত করেছে । কিছু কিছু ব্যাঙ্ক তাদের বিভিন্ন চার্জ চার গুণ পর্যন্ত বাড়িয়েছে, অতিরিক্ত মার্জিন আদায় করেছে । কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন চার্জ ও ফিস বেড়েছে ২০০% থেকে ৩০০% পর্যন্ত । সব মিলিয়ে ফিনান্সিয়াল কস্ট বেড়েছে প্রায় শতভাগ , যার প্রভাব পড়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর নিট মার্জিনে ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ৪৫% এর বেশি এসএমই ঋণ গ্রহীতা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন এবং ৩৮% শিল্প ঋণ গ্রহীতা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় হিমসিম খাচ্ছেন । এতে স্পষ্ট যে, কর্পোরেট গ্রাহকরা যেখানে অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধ করছে, সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আয়ের শীর্ষে অবস্থান করছে । এটি একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈপরীত্য বলেই মনে হচ্ছে ।
ব্যাংক ও কর্পোরেট খাতের সম্পর্ক মূলত হওয়া উচিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে । কিন্তু বাস্তবচিত্র বলছে ভিন্ন কথা । বেশিরভাগ ব্যাংক ডলার রেটের ওঠানামাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে, আমদানিকারকদের রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ রয়েছে । প্রসেসিং ফি ও সার্ভিস চার্জ ধার্য করা হয়েছে অনেক সময় কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড ছাড়াই । অনানুষ্ঠানিক ডলার প্রিমিয়াম আদায় করা হয়েছে, যা বাণিজ্যিক নীতিমালার লঙ্ঘন । ব্যাংক কর্মকর্তারা রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টের পরিবর্তে সেলস টার্গেট পূরণে বেশি মনোযোগী হয়েছেন, যার ফলে কর্পোরেট ক্লায়েন্টরা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । বাংলাদেশ ব্যাংকের অপ্রতুল তদারকি এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এসব অস্পষ্ট লেনদেন বাড়ছে ।
এই অসম্যের পরিণতি কী হতে পারে?
১. উৎপাদন খাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা আসতে পারে । শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান অব্যাহত থাকলে বিনিয়োগকারীরা উৎপাদন খাতে আগ্রহ হারাবে ।
২. আর্থিক চাপের কারণে কোম্পানিগুলো কর্মী ছাঁটাইয়ে বাধ্য হবে, ফলে চাকরিচ্যুতি ও বেকারত্ব বাড়বে ।
৩. অধিক আর্থিক খরচের কারণে রপ্তানিকারকরা বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা হারাবে এবং রপ্তানি হ্রাস পাবে ।
৪. সর্বোপরি, ব্যাংকিং খাতে আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে । গ্রাহকেরা যদি ব্যাংক ব্যাবস্থায় আস্থার অভাব দেখেন, তাহলে তারা বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজবে, যা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে ।
সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ
১. নৈতিক ব্যাংকিং নীতিমালা কার্যকর করা: বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে একটি নৈতিক ব্যাংকিং গাইডলাইন জারি করা উচিত, যা অতিরিক্ত চার্জ, অস্বচ্ছ ডলার প্রিমিয়াম এবং জোরপূর্বক সেবা বিক্রিকে নিষিদ্ধ করবে ।
২. সুদের হার যৌক্তিকীকরণ: প্রয়োজনীয় উৎপাদন, কৃষি ও রপ্তানিমুখী খাতের জন্য নিম্ন সুদে ঋণ প্রদান, নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা সূচকের সাথে সংযুক্ত করে প্রণোদনা ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা উচিত ।
৩. ফি ও চার্জের স্বচ্ছতা: সমস্ত ব্যাংককে বাধ্যতামূলকভাবে যৌক্তিক সার্ভিস চার্জ নির্ধারন করতে হবে ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হলে তার যৌক্তিকতা প্রমান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে ।
৪. শক্তিশালী অভিযোগ ও নিবারণ সেল গঠন: একটি কার্যকর ও স্বতন্ত্র ব্যাংকিং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গড়ে তোলা জরুরি, যেখানে কর্পোরেট ক্লায়েন্টরা নির্ভয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং প্রতিকার পাবেন ।
৫. বৈদেশিক মুদ্রা হারের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য নির্ধারণ: ইন্টারব্যাংক ও ক্লায়েন্ট রেটের মাঝে সর্বোচ্চ অনুমোদিত ডিফারেন্স নির্ধারণ করে অতিরিক্ত লভ্যাংশ আদায় রোধ করতে হবে । সংযত কারণে, লোকসান হলে ব্যাংক ক্লায়েন্ট হাড়াহাড়ি ভাগে বহন করতে হবে ।
৬. সম্পর্কভিত্তিক ব্যাংকিং সংস্কৃতি গড়ে তোলা: ব্যাংকগুলোর উচিত ঝুঁকি ভাগাভাগির ভিত্তিতে ক্লায়েন্টের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা, যেখানে ক্লায়েন্টের স্থায়িত্ব ও মুনাফা উভয়ই বিবেচনায় নেওয়া হবে ।
পরিশেষ
ব্যাংক ও কর্পোরেট খাতের মধ্যকার এই বৈপরীত্য শুধু অর্থনৈতিক সংকেত নয়, এটি আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি দূর্বলতা প্রকাশ করে । যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও শিল্প বিকাশের মাধ্যমে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এগোতে চায়, সেখানে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা হতে হবে দায়িত্বশীল ও নৈতিক । স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও উন্নয়নমুখী ব্যাংকিং চর্চা কেবল নীতি নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের ভিত্তি । ব্যাংকগুলোর উচিত ক্লায়েন্টদের উন্নয়নমুখী আর্থিক অংশীদার অংশীদার হিসেবে দেখা । সুদের হার, সার্ভিস চার্জ বা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন- সবকিছুতেই স্বচ্ছতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি । ব্যাংকগুলোর উচিত গ্রাহকদের শুধু ক্লায়েন্ট হিসেবে না দেখে অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা ।
বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেবল মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান না হয়ে উন্নয়নমুখী আর্থিক অংশীদার হিসেবে গড়ে উঠতে হবে । যৌক্তিক মুনাফা অবশ্যই দরকার, তবে তা যেন সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য ও জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে না যায় । ব্যাংক ও কর্পোরেট খাত পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয় । ব্যাংকগুলো যদি শুধু নিজেদের লাভের কথা ভাবে, তাহলে কর্পোরেট গ্রাহকরা ধীরে ধীরে আস্থা হারাবে। একটি উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা হওয়া উচিত আরও দায়িত্বশীল যেখানে সামাজিক ন্যায্যতা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় । একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ব্যাংক ও কর্পোরেট খাতকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে হবে। যৌক্তিক মুনাফা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষাও সমান জরুরি ।
লেখক: মোঃ আল-আমিন ভূঁঞা
কর্পোরেট ফাইন্যান্স এবং অর্থনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক ।




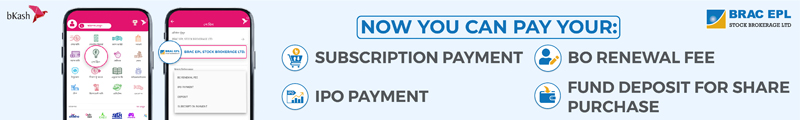
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.